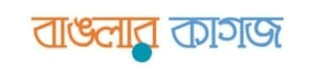মুক্তিযোদ্ধার বিজয়গাঁথা : দেবেশ চন্দ্র সান্যাল

বীর মুক্তিযোদ্ধার কলাম : : ১৯৭১ সালে আমি রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর কালোরাত থেকে শুরু হলো পাকস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতা। ওরা এই বিশ্বের জঘন্যতম নৃশংসতার নাম দিলো ‘অপারেশন সার্চলাইট’। ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর চালালো বিনা বিচারে জ্বালাও-পোড়াও, নির্যাতন আর হত্যা। পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংসতার সংবাদ পেয়ে বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও বাণী প্রদান করলেন। দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানালেন। বললেন, ... শেষ পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।
২৫ মার্চ ১৯৭১ এর পর আস্তে আস্তে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা সারাদেশের অধিকাংশ জায়গায় ক্যাম্প করলো। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে হেরে যাওয়া জামায়াতে ইসলাম, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতাকর্মীরা পাকিস্তানের পক্ষ নিলো। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের সহযোগিতার জন্য পিস কমিটি (শান্তি কমিটি), রাজাকার, আল বদর, আল শামস্ ও অন্যান্য বাহিনী গড়ে তুললো। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বিহারী যুবকদের ‘হিন্দুদের শায়েস্তা করতে হবে’ বলে সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং দিয়ে এ দেশে নিয়ে এসেছিলো। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের এ দেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় সারাদেশব্যাপী জ্বালাও-পোড়াও, হত্যা, গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণসহ বিভিন্ন মানবতাবিরোধী কাজ করতে থাকলো। প্রতিদিন পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতার কথা জানতাম বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে।
উল্লাপাড়া থানার চড়িয়া ও কান সোনা ঘোষ পাড়া, সাথিঁয়া থানার ডেমড়া (বাউস গাড়ি রুপসী) ও করঞ্জায় গণহত্যা হলো। দেশের ভয়াবহ অবস্থা। পাকিস্তানি সৈন্যরা এক এক রাতে এক এক গ্রাম ঘিরে রেখে ভোর থেকে গণহত্যা চালায়। এ দেশীয় স্বাধীনতাবিরোধী সহযোগীদের দিয়ে লুটতরাজ চালায়। বাড়িঘর ও দোকানে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়। ২৫ মার্চ কালোরাতের পর থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং হিন্দুরা অনেকে ভারতে আশ্রয় নেন। বাঙালি সৈন্য, ইপিআর পুলিশ, আনসার ও অন্যান্যরা প্রতিরোধ যুদ্ধ চালায়। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ চালায়। পেশাদার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেকের আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কুলিয়ে উঠা সম্ভব হয় না। প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও সহযোগিতার জন্য বাঙালি সৈন্য ও অন্যান্যরা ভারতে আশ্রয় নেন।
আমাদের গ্রামে করতোয়া নদী পার হয়ে আসতে হবে। নৌপথ ছাড়া গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যরা আসতে পারবে না। আমাদের গ্রামের মুসলমান খুব ভালো। আমাদের গ্রামের সর্বজনাব ডা. জয়নুল আবেদিন সরকার (জতু ডাক্তার), ভাইস প্রিন্সিপাল নুরুল হক সরকার কেমিস্ট, নজরুল ইসলাম সরকার, ডা. খলিলুর রহমান, আব্দুল সরকার মৌলভী মোহাম্মদ হোসাইন, শাহ আলম মাস্টার, আব্দুল মজিদ সরকার, আবুল কালাম, আকবর আলী মোল্লা, ইউনুস মাস্টার, আকবর আলী প্রামাণিকসহ গ্রামের নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ মুসলমান যুবক ও সম্ভাব্য অন্যান্যদের ডেকে বললেন, ‘সারাদেশের ভয়াবহ অবস্থার কথা আপনারা সবাই জানেন। সারাদেশের যেখানে যাই হোক, সবাই দেখবেন আমাদের গ্রামের হিন্দুদের যেনো কোনও প্রকার ক্ষতি না হয়। হিন্দুরা আমাদের আমানত...। আমরা আমাদের গ্রামের হিন্দুদের রক্ষার জন্য সর্বাত্মক সতর্ক থাকবো।’
আমাদের গ্রামের একজন মানুষও পিস কমিটির সদস্য, রাজাকার কিংবা স্বাধীনতাবিরোধী হয় নাই। সব মুসলমনেরা হিন্দুদের জানমালের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। আমরা দিনরাত গ্রাম পাহারা শুরু করলাম। প্রতিবেশি মুসলমান যুবকেরা আমাদের সহযোগিতার জন্য সঙ্গে থাকলো। বড়দের নির্দেশে মজিদ, কালাম, নান্নু ও অন্যান্যরা রাতদিন পালা করে করে আমাদের সঙ্গে থেকে পাহারা দিলো। আমাদের পরিবার কয়েকদিন রাতে প্রতিবেশি মুসলমানদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ঘুমাতাম। আমাদের গ্রামের মুসলমানেরা এতো ভালো যে, তাঁরা আমাদের জন্য ঘর ও বিছানা ছেড়ে দিয়ে নিজেরা বারান্দায় ঘুমাতেন। আমরা কয়েকদিন গ্রামের বাড়ি ছেড়ে আমাদের গ্রাম অপেক্ষা আরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বাচড়া গ্রামের এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকলাম। একাকী মনে মনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম। মানুষের বাড়িতে আর কতো দিন থাকা যায়? আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে গ্রামের বাড়িতে ফিলে এলাম। রাতদিন পালা করে করে পাড়া (গ্রামের অংশ) পাহারা দিতে থাকলাম। আর মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পথ খুঁজতে থাকলাম।
শ্রাবণ মাসের প্রথমদিক। দিনটি ছিলো ৬ শ্রাবণ ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ ও ২৩ জুলাই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ (শুক্রবার)। বর্ষাকাল। রাত ৮টার দিকে দেখি আমাদের বাড়ির অদূরে পালেদের বিলে দুইটি ছইওয়ালা নৌকা। নৌকা দেখে এগিয়ে গেলাম। বাচড়া গ্রামের আমার পরিচিত আব্দুল ওহাবকে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম। কী হবে? ওহাব বললো, এমপিএ জনাব আব্দুর রহমান স্যার এলাকার ইচ্ছুকদের মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংয়ের জন্য ভারত নিয়ে যাচ্ছেন। আমি বলাম, তাহলে আমিও যাবো। আমি চলে এলাম বাড়িতে। গোপনে আমার জামাকাপড় গোছালাম, তারপর আমার পড়ার খাতার একটি পৃষ্ঠা ছিড়ে মাকে উদ্দেশ করে একটি চিরকুট লিখলাম। চিরকুটটি ছিলো, ‘মা, প্রণাম নিও, বাবাকে আমার প্রণাম দিও। বড় দাদা, মেজোদাদা ও বৌদিকে প্রণাম দিও। ছোট ভাই-বোনকে স্নেহাশিস দিও। আমি মুক্তিযুদ্ধে গেলাম। তোমাদেরকে বলে গেলে যেতে দিতে না জন্য না বলে চলে গেলাম। অপরাধ ক্ষমা করিও। আশীর্বাদ করিও। আমি যেনো বিজয়ী হয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারি। ইতি, তোমার ছেলে দেবেশ।’
দিনটি ছিলো আমাদের গ্রামের হাটবার। পিতৃদেব হাট থেকে ভালো মাছ এনেছেন, মাতৃদেবী রান্না করছেন। আর কিছুক্ষণ পরেই আমাদের সবাইকে খেতে ডাকবেন। আমি বাড়ির কাউকে না বলে গোপনে নৌকায় গিয়ে বসলাম। রাত ৮টা ৩০ মিনিটের দিকে শাহজাদপুরের রাজ্জাক ও এরশাদ ভাইসহ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে একটা নৌকায় এমপিএ জনাব আব্দুর রহমান স্যার এলেন। এমপিএ স্যারকে দেখে দেখা করার জন্য এগিয়ে গেলাম। সামনে দাঁড়িয়ে আদাব দিলাম। আমাকে দেখে স্যার বললেন, ‘দেবেশ, তুমি কেনো?’ এতো ছোট মানুষকে তো মুক্তিযুদ্ধে নিবে না। আমি অনুরোধ করলাম। এমপিএ স্যার বললেন, ঠিক আছে চলো। তারপর রতন কান্দি পালেদের বিলের ঘাট থেকে রাত ৯টার দিকে আমাদের নৌকা ছাড়লো। মানসিকভাবে ভগবানকে প্রণাম করলাম। শুরু হলো এক কিশোরের জীবনপণ যুদ্ধে যাওয়া। আমরা সুজানগর সাত বাড়িয়া হয়ে পদ্মা নদী পাড় হয়ে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার চিলমারি ইউনিয়নের খারিজাথাক গ্রাম দিয়ে বাংলাদেশের বর্ডার অতিক্রম করলাম। আমরা ভারতের পশ্চিম বাংলার জলঙ্গী বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢুকলাম। একটি বিএসএফ ক্যাম্পে ঢুকলাম। প্রাতঃক্রিয়াদি শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। এমপিএ স্যার ও আমাদের গাইডারকে একটি চেয়ারে বসতে দিলেন। আমাদের সবাইকে এক লাইনে দাঁড় করালেন। আমাদের গণনা করা হলো। আমরা হলাম ২২ জন। এমপিএ স্যার আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণের কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি অস্থায়ী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে কলিকাতা চলে গেলেন। আমরা রাত ৯টার দিকে কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছালাম। তাঁরা আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন সকালে আমাদের সবাইকে ফলোইং করালেন। বয়সের স্বল্পতার কারণে ট্রেনিং কর্তৃপক্ষ আমাকে ভর্তি করতে চাইলেন না। নিরুপায় হয়ে আমি আমার ওল্ড মালদহের পিশে মহাশয় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তখন ভারতীয়রা বাংলাদেশের লোকদেরকে ‘জয় বাংলার’ লোক বলতো। ভারতের ট্রেন ও বাসে বাংলাদেশের লোকের কোনও ভাড়া লাগতো না। বাস ও ট্রেনে ভাড়া চাইতে এলে ‘জয় বাংলা’ বললেই বুঝতে পারতেন আমরা বাংলাদেশের শরণার্থী। কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে একটি বাসে কাছাকাছি একটি রেল স্টেশনে গেলাম। তারপর ট্রেন ধরলাম। বারসই রেলওয়ে জংশন স্টেশন থেকে ট্রেন বদলাতে হলো। আমি স্টেশনে বসে আসি। মোবাইল কোর্টের লোক আমাকে ধরে নিয়ে গেলো। একটি রুমে বসালো। যাঁদের ট্রেনের টিকিট নাই, তাঁদের ম্যাজিস্ট্রেট এক এক করে ডেকে ডেকে জরিমানা করলো। পর্যায়ক্রমে আমার পালা এলো। আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম, ‘জয় বাংলা’। ওনারা বুঝতে পারলেন, আমি বাংলাদেশ থেকে গিয়েছি। আমাকে জরিমানা না করে ছেড়ে দিলেন। পরবর্তী ট্রেনে উঠে ওল্ড মালদহ স্টেশনে নেমে পিসে মহাশয় শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে গেলাম। কয়েকদিন ওল্ড মালদহ, গাজল, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি আত্মীয়ের বাড়ি ঘুরলাম। আমার পিশে মহাশয়ের ভগ্নিপতি ছিলেন একটি শরণার্থী ক্যাম্পের ইনচার্জ। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, ‘তুমি ছোট মানুষ, তোমার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে শরণার্থী ক্যাম্পে ভর্তি করে নিচ্ছি। তুমি রেশন, লারকি ও অন্যান্য সকল সুবিধা পাবে।’
আমি বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত এসে শরণার্থী শিবিরে বসে বসে খাবো- তাতে সম্মত হতে পারলাম না। আবার ফিরে এলাম কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে। আমাদের শাহজাদপুরের রবীন্দ্র নাথ বাগ্চী ও রতন কুমার দাসসহ কয়েকজনকে পেলাম। তাঁরা আমাকে পরামর্শ দিলেন তুমি মালঞ্চ (কুরমাইল) ক্যাম্পের ইনচার্জ ৭ নম্বর সেক্টরের উপদেষ্টা বেড়া সাঁথিয়ার এমএনএ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ স্যারের কাছে যাও। আমি তাঁদের পরামর্শে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ স্যারের কাছে গেলাম। আমার পরিচয় দিয়ে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আমাকে কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তি করার ব্যবস্থা করলেন। কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পের ভর্তি কর্তৃপক্ষকে আমাকে ভর্তি করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলাম। কর্তৃপক্ষ আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমার দেশপ্রেম, সাহসী মনোভাব এবং অন্যান্য শুনে ভর্তি করালেন। প্রাথমিক ট্রেনিং ক্যাম্পে আমাদের ফলইং করিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ানো, পিটি প্যারেড করানো হতো।
ক’দিন কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে থাকার পর আমাকে, রবীন্দ্র নাথ বাগ্চী, রতন কুমার দাস ও নজরুল ইসলামকে ট্রান্সফার করলো মালঞ্চ ট্রানজিট ক্যাম্পে। তারপর মালঞ্চ থেকে কুড়মাইল ট্রানজিট ক্যাম্পে। কুড়মাইল থেকে আমাদেরকে আনা হলো পতিরাম ক্যাম্পে। পতিরাম ক্যাম্প থেকে একযোগে ভারতীয় আর্মি লরিতে ২০/২২ জনকে নিয়ে আসা হলো দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার পানিঘাটা নামক ইন্ডিয়ান আর্মি ট্রেনিং ক্যাম্পে। প্রশিক্ষণ শুরুর দিনে কো-অর্ডিনেটর প্রথমে ফলইং করিয়ে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন নিয়মকানুন বিষয়ে বললেন। তারপর তিনি বললেন, দুপুর ১২টায় প্রশিক্ষণ প্রধান ডি এস ভিলন স্যার আসবেন। ঠিক দুপুর ১২টায় প্রশিক্ষণ প্রধান শিখ সেনা ডি এস ভিলন স্যার এলেন। তিনি আমাদের সকলকে উদ্দেশ করে যা বললেন, তার অর্থ হলো, ‘... আপনাদেরকে স্যালুট। আপনারা বীর, আপনারা আপনাদের দেশমাতাকে হানাদারমুক্ত করতে যুদ্ধ করতে এসেছেন। আমরা আপনাদের জন্য তেমন কিছু করতে পারবো না। আমরা মানবিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিবো। আপনাদের দেশকে আপনাদেরই স্বাধীন করতে হবে। আপনাদের জন্মদাতা পিতা-মাতাকে স্যালুট জানাচ্ছি। তাঁরা দেশের জন্য তাঁদের সন্তানদেরকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন...।’
পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্পটি ছিলো ভারতের শিলিগুড়ি মহকুমার ৭ নম্বর সেক্টরের অধীন। পানিঘাটা স্থানটি ছিলো চারিদিকে পাহাড়ের মধ্যে। কার্শিয়ান পাহাড় হতে নেমে আসা একটি ক্যানেলের দক্ষিণ পাশের বনাঞ্চল। চাঁন মারি স্থানের বামপাশে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ঝর্ণার জল। ক্যাম্পে নিয়ে আমাদের তাবুর মধ্যে থাকার সিট করে দিলো। আমাদের প্রত্যেককে ১টা মগ, ১টা প্লেট, ২টা প্যান্ট, ২টা গেঞ্জি, ১টি মশারি ও বিছানাপত্র দেওয়া হলো। ট্রেনিং শুরু হলো। আমাদের ২১ দিনের ট্রেনিং হলো। আমাদেরকে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল, এলএমজি, এসএলআর, স্টেনগান, টুইঞ্চ মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ, এক্সপ্লোসিভের ব্যবহার, ফাস্ট এইডসহ অন্যান্য ট্রেনিং দিলো। যুদ্ধে সহযোদ্ধা আহত হলে বা শহিদ হলে করণীয় সর্ম্পকে এবং ফাস্ট এইড সম্পর্কে ধারণা দিলো। ভারতীয় কয়েকজন হিন্দু বিহারী ও শিখ সৈন্য প্রশিক্ষণ দিলেন আমাদের কোম্পানির। আমাদের কোম্পানির নাম ছিলো ডেল্টা কোম্পানি। প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন শিখ সেনা ডি এস ভিলন। এফএফ ধারী মুক্তিযোদ্ধাদের বিদায়ের পূর্বে স্লেটে চক দিয়ে এফএফ নম্বর লিখে বুকের উপর ধরিয়ে ছবি তোলা হতো। কিন্তু আমাদের কোম্পানির প্রশিক্ষণার্থীদের বিদায়ের পূর্বে ক’দিন ধরে বৃষ্টি হলো। আবহাওয়াজনিত কারণে আমাদের ছবি তুলতে পারলেন না। বিদায়ের সময়ে জানতে পারলাম, আমার এফএফ নম্বর : ৪৭৪২। ট্রেনিং শেষে ইন্ডিয়ান আর্মি ট্রাকযোগে আমাকে, রবীন্দ্র নাথ বাগ্চী, নজরুল ইসলাম ও রতন কুমার দাস ও অন্যান্য প্রায় ৫০ জনকে নিয়ে আসা হলো ৭ নম্বর সেক্টরের হেড কোয়ার্টার তরঙ্গপুরে। এটি ছিলো পশ্চিমবঙ্গের কালিয়াগঞ্জ থানার তরঙ্গপুর নামক স্থানে অবস্থিত। তরঙ্গপুর এনে সিরাজগঞ্জ জেলার ১০ জনের সমন্বয়ে একটি গেরিলা গ্রুপ করা হলো। আমাদের গ্রুপ লিডার নিযুক্ত হলেন বেলকুচি উপজেলার তামাই গ্রামের এম এ মান্নান। ডেপুটি লিডার নিযুক্ত হলেন শাহজাদপুর উপজেলার জামিরতা গ্রামের অধিবাসী বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগ্চী। আমাদেরকে তরঙ্গপুর থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ, রেশনিং ও পকেটমানি দেওয়া হলো। আমার নামে একটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল, এক ম্যাগজিন গুলি, একটি হেলমেট ইস্যু করা হলো। অন্যান্য গোলাবারুদ, মাইন, গ্রেনেড ও এক্সপ্লোসিভ কমান্ডার স্যারের কাছে দিলেন। মৃত্যু যে হবে না এমন কোনও গ্যারান্টি ছিলো না। তাই আমি মৃত্যুর প্রস্তুতি ও যুদ্ধ জয়ের জন্য তরঙ্গপুর বাজার থেকে একখানা শ্রী শ্রী চন্ডী গ্রন্থ, একটি মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও একটি ৪ ব্যান্ডের রেডিও কিনলাম। তরঙ্গপুর থেকে কালিয়াগঞ্জ পর্যন্ত বাসে এসে ট্রেনে উঠলাম। শিলিগুড়ি রেলওয়ে জংশন স্টেশনে এসে আমাদের ট্রেন বদলাতে হলো।
শিলিগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গ্রুপের সকলের সঙ্গে বসে আছি। দেখলাম, আমাদের প্ল্যাটফর্মের সামনের লাইনে একটি ফাঁকা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। আমি টয়লেট করার জন্য ট্রেনের একটি বাথরুমে ঢুকলাম। এমন অবস্থায় ট্রেনটি সার্ট করলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াহুড়া করে বাথরুম থেকে বের হয়ে লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর নেমে পড়লাম। আমার হাঁটুতে ব্যাথা লাগলো। আজ ভাবী, তখন পকেটে কোনও আইডি কার্ড ছিলো না। আমার অপরিচিত জায়গা, ওখানকার একজন মানুষও আমাকে চেনে না, আমি মারা গেলে আমার সাথীরাও আমাকে খুঁজে পেতেন না। আমার মা-বাবা সারাজীবন আমার পথপানে চেয়ে থাকতেন। আমার লাশটাও পেতেন না। পরে ট্রেন বদল করে আসামগামী ট্রেনে উঠলাম। আসামগামী ট্রেনে ধুপরী নামক স্টেশনে আমরা নামলাম। তারপর বাসযোগে মানিকার চর এলাম। রাত হয়ে যাবার কারণে রাতে মানিকার চর একটা ভাড়া বোর্ডিংয়ে থাকলাম। পরদিন সকালে মানিকার চর থেকে নদী পার হয়ে এলাম তদানীন্তন রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার (বর্তমানে জেলা) মুক্তাঞ্চলে স্থাপিত রৌমারী মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। রৌমারী ক্যাম্পে আমরা স্নান, খাওয়া-দাওয়া করলাম। আমাদের কমান্ডার স্যার সিরাজগঞ্জ জেলার মুক্তাঞ্চল যমুনার চড়ে পৌঁছানোর জন্য একটি বড় ছইওয়ালা নৌকা ভাড়া করলেন। রৌমারী ক্যাম্প থেকে রাতের খাবার খেয়ে রাত ৯টার দিকে আমাদের নৌকা ছাড়লো। ওই দিনটি ছিলো : ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ।
নৌকা বাহাদূরাবাদ ঘাট, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা দিয়ে আসতে হয়। আমরা জানতে পেরেছিলাম, বাহাদূরাবাদ ঘাট অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। ওই ক্যাম্পের পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারেরা ভয়ানক। তারা স্পিডবোট নিয়ে রাতে নদী টইল দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা পেলে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।
আমাদের কমান্ডার জনাব এম এ মান্নান স্যার নির্দেশ দিলেন, ‘আপনারা সবাই নৌকার ডওরার মধ্যে পজিশন অবস্থায় থাকুন। পাকিস্তানি হানাদারেরা ধরতে এলে আমরা ধরা দিবো না। যুদ্ধ করবো। যুদ্ধ করে শহিদ হবো কিন্তু ওদের হাতে ধরা দিব না।’
রাত ২টার দিকে আমরা বাহাদূরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করতে থাকলাম। ওদের টর্চলাইটের আলো এসে বারবার আমাদের নৌকাতে পড়ছিলো। ভগবানের কৃপায়-ওরা আর স্পিডবোট নিয়ে ধরতে এলো না। আমরা বাহাদূরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করলাম। আমাদের সঙ্গে চিড়া গুড় ছিলো। ভোরে মাঝিরা এক কাইসা খেতের মধ্যে নৌকা ঢুকিয়ে দিলো। আমরা নিচে নেমে খেতের মধ্যে বাথরুম সারলাম। আমাদের সঙ্গে থাকা চিড়া ও গুড় দিয়ে সকালের জলখাবার খেলাম। তারপর নৌকা আবার ছাড়লো। তখন কাজিপুর থানার অধিকাংশ এলাকাসহ বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা পাকিস্তানি হানাদারদের দখলে। কাজিপুর থানার সম্মুখ দিয়ে আমাদের নৌকা আসবে। দেখেশুনে খোঁজ নিয়ে থামিয়ে থামিয়ে ৪ দিন ভরে নৌকা এসে পৌঁছালো সিরাজগঞ্জ হানাদার মুক্তাঞ্চল যমুনার চরে। এটি ছিলো টাঙ্গাইল জেলার সিংগুলির চড়ের নিকটবর্তী। নৌকাতেই রান্নার ব্যবস্থা ছিলো।
মাঝিরা কোনও রকমে ডাল-ভাত অথবা খিচুরি রান্না করে আমাদের খাওয়াতেন। এভাবে খেয়ে না খেয়ে চলছিলাম। পরদিন রাতে যমুনা নদীর এপাড়ে চলে এলাম। চলে এলাম বেলকুচি-কামারখন্দ নির্বাচনি এলাকার এমএনএ জনাব আব্দুল মোমিন তালুকদারের গ্রামের বাড়িতে। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর ভাই রশিদ তালুকদার আমাদের থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করলেন।
অক্টোবর, ১৯৭১ সালের মাঝামাঝির আগ পযর্ন্ত আমাদের গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যা কম থাকায় সম্মুখ যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত কমান্ডার স্যার নেন নি। আমরা পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ও তাদের দোসরদের আতঙ্কে রাখার জন্য গেরিলা কার্যক্রম ‘হিট অ্যান্ড রান’ চালাতাম। পাকিস্তানি সৈন্য বা রাজাকার ক্যাম্পের নিকটবর্তী গিয়ে ২/৪টা থ্রি-নট-থ্র্রি রাইফেলের আকাশমুখী ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে চলে আসতাম। পাকিস্তানি দালাল, পিস কমিটির লোক ও অন্যান্যরা আমাদের অস্তিস্তের কথা জানতে পারতো। আমরা দিনের বেলা স্কুলে বা কারও বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতাম। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশের অভ্যন্তরে ছিলো দুইটি পক্ষ। একটি স্বাধীনতার পক্ষে, অন্যটি স্বাধীনতার বিপক্ষে। স্বাধীনতার বিপক্ষের পিস কমিটির সদস্য, রাজাকার, আল বদর, আল শামস্ ও অন্যান্যরা। স্বাধীনতাবিরোধীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে এসে বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও চাঁদাবাজি করতো। বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে নির্যাতন ও হত্যা করতো। হিন্দু ও আওয়ামী লীগ নেতারা ছিলো ওদের বড় টার্গেট। হিন্দু নারী পুরুষকে ধরে নিয়ে যেতো। নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা করতো। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারাও অত্যাচারী পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকারদের হত্যা করতো। গণহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য মানবতাবিরোধী কাজে সরাসরি জড়িত কোনও পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যকে ধরতে পারলে ফায়ারিং স্কোয়াডে বিচার করার পরিকল্পনা ছিলো। যে কারণে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপে সাহসী একজনকে জল্লাদ হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিলো। আমাদের গ্রুপের জল্লাদ হিসেবে মনোনীত ছিলেন দৌলতপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হক। আমরা এমন কোনও পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ধরতে পারি নাই। আমরা কখনো কাউকে মারি নাই। আমাদের গ্রুপের নীতি ছিলো, আমরা আমাদের দেশি কোনও লোককে হত্যা করবো না। বুঝিয়ে তাদেরকে স্বাধীনতার পক্ষে আনবো। যে কারণে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ কোনও স্বাধীনতাবিরোধীকে ধরি নাই, অত্যাচার বা হত্যা করি নাই। আমরা নিজেরা বা তাদের আত্মীয়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে বিভিন্নভাবে স্বাধীনতাবিরোধীদের স্বাধীনতার পক্ষে আনার চেষ্টা করতাম। আমরা প্রতিটি মুহূর্তে আতঙ্কে থাকতাম। যে কোনও সময় পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আমাদের থাকা-খাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা ছিলো না। আমরা আজ এ শেল্টারে তো কাল সে শেল্টারে থাকতাম। কোন শেল্টারেই একাধিক দিন থাকতাম না। কোনও কোনও দিন শেল্টারের অভাবে সারারাত চিড়া-গুড় খেয়ে রাত্রি জেগে স্কুলের বেঞ্চে শুয়ে থাকতে হতো। কি যে অমানবিক কষ্ট। আমাদের শেল্টার পালাক্রমে আমরা দু’জন করে করে পাহারা দিতাম। প্রতিরাতে কমান্ডার স্যার আমাদের বিশেষ নির্দেশ দিতেন। আমরা রাতে বিভিন্ন রাজাকারের বাড়িতে গিয়ে তাদের বুঝাতাম। সকালে আমরা অস্ত্রে ফুল থ্রু মারতাম, পরিস্কার করতাম ও অস্ত্রে তেল দিতাম। তখন দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিলো স্বাধীনতার পক্ষে। তবুও স্বাধীনতাবিরোধীদের ভয়ে অনেকে আমাদেরকে শেল্টার বা খাবার দিতে সাহস পেতেন না। কারণ অধিকাংশ গ্রামেই ছিলো পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকার। তারা খোঁজ জানলে পাশের আর্মি বা রাজাকার ক্যাম্পে সংবাদ দিয়ে পাকিস্তানিদের নিয়ে এসে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে, বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে হত্যা করবে ও অত্যাচার চালাবে- এই ছিলো সাধারণ মানুষের ভয়।
আমাদের সঙ্গে সব সময় চিড়াগুড় থাকতো। স্থানীয় কিছু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ট্রেনিং দিয়ে আমাদের সঙ্গে নিলাম। আমি মুক্তিযুদ্ধে যাবার কারণে আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। একটি অবুঝ কিশোর ছেলের পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! আমাকে খুঁজে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ও রাজাকারদের আলটিমেটামে গণহত্যার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গোটা পরিবার বাড়িঘর সব ফেলে ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে ভারতের আসামের মানিকার চড় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।
কোথাও আক্রমণের পূর্বে আমরা রেকি করে দেখতাম। তারপর আক্রমণ করতাম। আমি আমার গ্রুপ কমান্ডার ও রণাঙ্গণের সাথীদের বলে রেখে ছিলাম, ‘আমি রণাঙ্গণে মারা গেলে, তরঙ্গপুর বাজার থেকে কেনা জাতীয় পতাকা দিয়ে মুড়িয়ে আমার দেহ নদীতে দিয়ে দিবেন।’
মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে আমি মারা গেলে, তখন লাশ নিয়ে অন্ত্যেষ্টি করার কোনও লোক ছিলো না। আমাদের গ্রুপের গেরিলা-সম্মুখ যুদ্ধগুলো হলো :
১) বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধ : বেলকুচি সিরাজগঞ্জ জেলার একটি উল্লেখযোগ্য থানা। অক্টোবর, ১৯৭১ সালের শেষের দিকে আমরা এই থানা আক্রমণ করেছিলাম। এই থানা আক্রমণ যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন আমাদের গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম এ মান্নান স্যার। কমান্ডার স্যার এবং আরও ৩ জনের রেকিতে একযোগে বেলকুচি থানা ও মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল মতিনের বাড়ি আক্রমণ করলাম। সন্ধ্যায় বানিয়া গাতি গ্রামের এক বাড়ির শেল্টারে কমান্ডার স্যার বিস্তারিত ব্রিফ করলেন। আমাদের দুই গ্রুপে ভাগ করে দিলেন। সিদ্ধান্ত হলো : কমান্ডার স্যারের নেতৃত্বে বড় গ্রুপটি থানা আক্রমণ করবে, অন্য গ্রুপটি রবীন্দ্র নাথ বাগ্চীর নেতৃত্বে মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করে মতিন সাহেবকে ধরে আনবে। আমি কমান্ডার স্যারের গ্রুপে থেকে থানা আক্রমণ যুদ্ধে অংশ নিলাম। রাত ৯টায় বানিয়া গাতি থেকে যাত্রা করলাম। থানার কাছে গিয়ে দু গ্রুপ টার্গেটের উদ্দেশ্যে ভাগ হয়ে গেলাম। নিদিষ্ট সময়ে রাত ১২টায় একযোগে আক্রমণের সিদ্ধান্ত হলো। পরিকল্পনা মোতাবেক থানার পশ্চিম পাশ দিয়ে স্ক্রোলিং করে থানার সামনে যেতেই সেন্ট্রি দেখে ফেললো। হুইসেল বাঁজিয়ে থানার সবাইকে জানিয়ে দিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি চালালো। আমাদের কমান্ডার স্যার কমান্ড করে ফায়ার ওপেন করলেন। আমরা সবাই একযোগে গুলি করলাম। একঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধ চললো। ভয়াবহ যুদ্ধ। আমার মাথায় হেলমেট। দুইটি গুলি এসে হেলমেটে লাগলো। আমার ডান পাশে আমার কমান্ডার। হয় বিজয় আর না হয় মৃত্যু ছাড়া কোনও পথ নাই। বৃষ্টির মতো গুলি চালিয়ে যাচ্ছি। যুদ্ধের এক সময়ে কমান্ডার স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘দেবেশ মাথা তুলো না, গুলি চালিয়ে যাও।’
আমাদের বৃষ্টির মতো গুলিতে থানার বিহারী পুলিশ ও রাজাকার থানার পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে সোহাগপুর নদীতে থাকা একটি লঞ্চে চড়ে আমাদের রেঞ্জের বাইরে যমুনার মধ্যে চলে গেলো। থানার সেন্ট্রি গুলি করা বন্ধ করে দুই হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণ করলো।
আমরা থানার ভিতরে ঢুকে পড়লাম। আমরা থানার মালখানা থেকে সকল গোলাবারুদ নিলাম। থানার দু’জন রাজাকারকে জ্যান্ত বেঁধে ধরে নিয়ে এলাম। রাজাকাররা যাতে আমাদের শেল্টার চিনতে না পারে, সেজন্য তাদের চোখ বেঁধে নিয়ে এলাম। ভোর হয়ে গেলো। মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করা দলটিও এলো। মতিন সাহেব পালিয়ে গেছে। তাকে ধরা সম্ভব হয় নাই। থানার আশেপাশের লোকজন দোকান ও বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিলো। বিজয়ী হয়ে চলে এলাম।
পরদিন সিরাজগঞ্জ থেকে শতাধিক পাকি হানাদার ও রাজাকার এসে থানার আশেপাশে আগুন দিয়েছিলো এবং মানুষদের নির্যাতন করেছিলো। বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধে আমরা ২ জন রাজাকারকে ধরে এনেছিলাম। কিছু সময় চোখ বেঁধে আমাদের শেল্টারের ও আলাদা রুমে রেখেছিলাম। তাদেরকে চোখ বেঁধে পাশের রুমে রাখা হয়েছিলো। আমি কমান্ডার স্যারের অনুমতি নিয়ে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। তাদেরকে রাজাকার হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম ও শুনলাম। ওদের জিজ্ঞাসাবাদে মনে হলো, ওরা সহজ সরল ও অভাবী মানুষ। ওদের বাড়িতে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা আছে। পিস কমিটির লোকদের কথায় বিশ্বাস করে ওরা রাজাকার হয়েছে। ওরা মনে করেছিলো, এটা একটা চাকুরি। উপার্জন করে সংসার পরিচালনার জন্য ওরা রাজাকার হয়েছে। তারা বললো, আমরা কাউকে কোনও অত্যাচার করি নাই। কোনও বাড়িঘর লুটতরাজ করি নাই। পাকিস্তানি হানাদারদের নিয়ে এসে কোনও গণহত্যা করি নাই। কোনও বাড়িতে আগুন দিই নাই...। তাদের কথায় আমার মায়া হলো। আমি তাদের চোখ বাঁধা খুলে দিলাম। তাদেরকে বিভিন্নভাবে বোঝালাম। রাতে শেল্টার পরিবর্তনের সময় কমান্ডার স্যারকে অনুরোধ করে রাজাকার দুইজনকে ছেড়ে দিয়েছিলাম।
২) কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশনে পাকিস্তানি সৈন্য ও ব্রিজ পাহারারত রাজাকারদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করার জন্য অ্যাম্বুস : কালিয়া হরিপুর সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ থানার একটি রেলওয়ে স্টেশন। এই অ্যাম্বুসের নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম এ মান্নান স্যার। ৪ নভেম্বর, ১৯৭১ সালে আমাদের গ্রুপের ঝাঐল গ্রামের সিরাজগঞ্জের এমএনএ জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদারের ভায়রা আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুল হামিদ তালুকদারের রেকির ভিত্তিতে কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশনে পাকিস্তানি সৈন্য ও ব্রিজ পাহারারত রাজাকারদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করার জন্য অ্যাম্বুস করেছিলাম। কালিয়া হরিপুর যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমার রণাঙ্গনের সাথী জনাব আব্দুল হামিদ তালুকদার সাহেব বললেন, ‘দেবেশ, মানিকাচর তোমার বাবা-মাসহ পরিবারের সবার সঙ্গে দেখা করেছি। সবাই ভালো আছেন। তোমার রেশন ও পকেট মানির টাকা তোমার আব্বার হাতে দিয়ে এসেছি। তোমার এক ভাই আমার সঙ্গে এসেছে, তাঁকে শমেসপুর গ্রামে এক বাড়িতে রেখে এসেছি। আগামীকাল সে তোমার কাছে আসবে।’
ওই অ্যাম্বুস যুদ্ধ হয় নাই। কমান্ডার স্যার স্ক্রোলিং করে রেললাইনে বৈদ্যুতিক মাইন বসিয়ে এসেছিলেন। তথ্য ছিলো ঈশ্বরদী থেকে পাকি হানাদার নিয়ে একটি ট্রেন সিরাজগঞ্জ যাবে। কমান্ডার স্যার ট্রেনটি উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন। আমরা ধানক্ষেতের মধ্যে পজিশন অবস্থায় থাকলাম। কামান্ডার স্যারের হাতে মাইনের তার ও ব্যাটারি। টর্চলাইট ও হ্যারিকেন হাতে পাকি মিলিশিয়া ও রাজাকারেরা স্টেশনে টহল দিচ্ছিলো। ওদের পায়ে লেগে হঠাৎ আমাদের মাইনের তার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। মাইনটি ওদের নজরে পড়লো। হুইসেল দিয়ে রাজাকারদের পজিশনে রেডি থাকতে বললো। আমাদের দিকে টর্চলাইট মেরে মেরে উর্দুতে বকাবকি করতে থাকলো।
ইতিমধ্যে ঈশ্বরদী থেকে সিরাজগঞ্জগামী পাকি হানাদারবাহী ট্রেন এলো। পাকি হানাদারেরা সিগন্যাল দিলো। তারা স্টেশনে ট্রেনটি থামিয়ে দিলো। ট্রেনের পাকি হানাদারেরা অস্ত্র তাক করা অবস্থায় নেমে আমাদেরকে খুঁজতে থাকলো। মাইনের বৈদ্যুতিক তার বিছিন্ন হয়ে পরায় আমাদের মাইনটি ব্রাস্ট করা সম্ভব হলো না। পাকি হানাদারদের সংখ্যাধিক্যতায় ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় কমান্ডার স্যার উইথড্র হওয়ার কমান্ড করলেন। আমরা উইথড্র হয়ে কমান্ডার স্যারের বাড়ি বেলকুচি থানার তামাই গ্রামে এলাম। পরেরদিন সিরাজগঞ্জ থেকে পাকি হানাদার ও রাজাকারেরা এসে কালিয়া হরিপুর ও পাশের কয়েকটি গ্রামের কয়েকটি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিলো। কিছু লোকের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলো। আমরা কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশন অ্যাম্বুস থেকে ফিরে এসে তামাই গ্রামে কমান্ডার স্যারের বাড়িতে একত্রিত হই। কমান্ডার স্যারের মা আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা কমান্ডার স্যারের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের সবাইকে বসিয়ে কমান্ডার স্যার ব্রিফ করলেন। স্থানীয়ভাবে ট্রেনিং দেওয়া বেশকিছু যুবককে আমাদের গ্রুপে ভর্তি করা হলো। এতো বড় প্লাটুন এক শেল্টারে, শেল্টার নেওয়া সমস্যা হলো। তাই কমান্ডার স্যার ডেপুটি কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগ্চীকে কমান্ডার করে আমাদের ১১ জনের আর একটি গ্রুপ করে দিলেন।
৩) কল্যাণপুর যুদ্ধ : কল্যাণপুর সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার একটি গ্রাম। ৫ নভেম্বর, ১৯৭১ এ কল্যাণপুর গ্রামে একটি যুদ্ধ হয়েছিলো। এই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার (কমান্ডার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত) বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগ্চী। কমান্ডার স্যারের নির্দেশে আমরা ১১ জন রবীন্দ্র নাথ বাগ্চীর কমান্ডনাধীন হয়ে হেঁটে ভোরে বেলকুচি উপজেলার কল্যাণপুর নামক গ্রামে এক বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। বাড়ির মালিক আমাদের সকালের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমরা সারারাত নিদ্রাহীন থেকে ও হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সকালের খাবার খেয়ে প্রকাশ্যে পিটি-প্যারেড করলাম। অস্ত্র পরিষ্কার করলাম। অস্ত্রে ফুলথ্রু মারলাম। একজন করে করে আমাদের অবস্থান পাহারা দিতে থাকলাম। অন্যান্যরা কেউ কেউ ঘুম বা রেস্টে থাকলাম। কল্যাণপুর একটি নিভৃত গ্রাম। আমাদের ধারণা ছিলো, এই গ্রামে পাকি হানাদার ও রাজাকার আসবে না। বেলা ১০টার দিকে সেন্ট্রিরত সহযোদ্ধা রতনকুমার দাস দৌড়ে এসে জানালেন আমাদেরকে ধরার জন্য বেলকুচি থানা থেকে কয়েকজন পাকি হানাদার মিলিশিয়া ও রাজাকার আসছে। বওড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে কল্যাণপুরের দিকে আসছে। দুইজন পাকিস্তানি দালাল গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে নিয়ে হানাদার ও রাজাকারদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসছে। দূর থেকে অনুমান হলো এই দলে ৫জন মিলিশিয়া ও ৪ জন রাজাকার আছে। আমাদের কমান্ডার যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা কল্যাণপুরে রাস্তার ধারে বাঁশঝাড়ের মধ্যে পজিশন নিলাম। বাঁশঝাড়ের সামনে দিয়ে চলা রাস্তা ধরে পাকিস্তানি হানাদার ও রাজাকারেরা আসছিলো। আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগ্চী কমান্ড ও ফায়ার ওপেন করলেন। আমরা একযোগে গুলি করা শুরু করলাম। এক লাফে হানাদারেরা রাস্তার উত্তরপাশে পজিশন নিলো। ওরাও আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালালো। আমরাও একযোগে বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়তে থাকলাম। গোলাগুলির শব্দ পেয়ে আশপাশে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এলো। এক ঘণ্টারও অধিক সময় সম্মুখ যুদ্ধ চললো। তারপর পাকি হানাদারেরা পিছিয়ে গেলো। যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমরা বিজয় উল্লাস করলাম। সকল স্তরের মানুষের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হলো। এক বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করলাম। তারপর হেঁটে দৌলতপুর গ্রামের সহযোদ্ধা মুক্তি শামসুল হকের বাড়িতে শেল্টার নিলাম। ১৪ নভেম্বর, ১৯৭১ সালে এই শেল্টারে আমার মেজো দাদা সমরেন্দ্র নাথ সান্যাল আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কয়েকদিন দৌলতপুর, তেঞাশিয়া, খুকনী, বাজিয়ারপাড়া, দরগার চর ও অন্যান্য গ্রামে থাকতে লাগলাম।
৪) ধীতপুর যুদ্ধ : ধীতপুর সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার একটি গ্রাম। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার (কমান্ডার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত) বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগ্চী। ডিসেম্বর, ১৯৭১ এর প্রথম সপ্তাহের পর আমরা শেল্টার নিলাম সৈয়দপুর গ্রামের কালা চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্যদের বাড়িতে। ১৩ ডিসেম্বর সংবাদ পেলাম পাকি হানাদারেরা কৈজুরী হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। টাঙ্গাইলের যুদ্ধে পাকি হানাদারেরা পরাজিত হয়ে লঞ্চে যমুনা নদী পার হয়ে মালিপাড়া ক্যাম্পে এসেছে। মালিপাড়া ক্যাম্প থেকে রাস্তা চিনানোর জন্য দুইজন রাজাকারকে সঙ্গে নিয়েছে। আমরা পাকি হানাদারদের আক্রমণ করার জন্য ওদের পিছু নিলাম। সংবাদ পেয়ে শাহজাদপুুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপগুলোও আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে এলো। পাকি হানাদারেরা ছিলো ক্ষুধার্ত। কৈজুরী গ্রামের একজনের মূলা ক্ষেত থেকে মূলা খাওয়ার চেষ্টা করলো। ওরা হয়তো জানতো না কাঁচা মূলা খাওয়া যায় না।
ওয়াপদা বাঁধ ধরে ওরা অগ্রসর হতে লাগলো। আমরাও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অস্ত্র তাক করে ওদের পিছু পিছু হাটতে থাকলাম। ওরা ভীষণ ক্রোধি। ধীতপুর নামক স্থানে গিয়ে ওরা আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করলো। আমরা জাম্প করে ওয়াপদা বাঁধের পশ্চিমদিকে পজিশন নিলাম। ওদের উপর গুলি ছুড়তে শুরু করলাম। ওরা ওয়াপদা বাঁধের পূর্বপাশে পজিশন নিলো। একঘণ্টা ব্যাপী গুলি-পাল্টা গুলি চলতে থাকলো। গুলির শব্দে বেড়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা দল আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এলো। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। হানাদারেরা গুলি করা বন্ধ করলো। আমরাও অন্ধকারে গুলি করা বন্ধ করলাম। সারারাত আমরা না খেয়ে পজিশন অবস্থায় ছিলাম। আমাদের গ্রুপটি ছিলো বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগ্চীর কমান্ডানাধীন। আমার বামপাশের এলএমজি চালাচ্ছিলেন কমান্ডার রবীন্দ্র নাথা বাগ্চী স্যার। আমার ডানপাশের থ্রি-নট-থ্রি চালাচ্ছিলেন আমার মেজো দাদা সমরেন্দ্র নাথ সান্যাল, তাঁর ডানপাশে আমার গ্রুপের অন্যান্যরা স্টেনগান ও থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল চালাচ্ছিলেন। যুদ্ধটি ছিলো ভীষণ ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ। তথাকথিত হিংস্র পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।
সন্ধ্যার পর ওরা গুলি করা বন্ধ করলো, আমরাও গুলি করা বন্ধ করলাম। হয় যুদ্ধে বিজয়ী হতে হবে, অন্যথায় সবার জীবন যাবে। রাতে ধীতপুর সার গুদাম থেকে মাঝে মাঝে ২/১টা করে গুলি আসছিলো। ওদের গুলির প্রেক্ষিতে আমরা ২/১টা করে গুলি করছিলাম। ভোরে আলো ফুঁটলে আমাদের কমান্ডার বরীন্দ্র নাথ বাগ্চী ও বেড়ার কমান্ডার এস এম আমির আলী ও অন্যান্যরা স্ক্রোলিং করে ধীতপুর সার গুদামে এগিয়ে গেলেন। সার গোডাউনে গিয়ে দেখা গেলো, দুজন রাজাকার সারারাত কভারিং ফায়ার করেছে। কমান্ড করে রাজাকার দু’জনকে স্যারেন্ডার করানো হলো। তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে নেওয়া হলো।
তাদের কাছ থেকে জানা গেলো, রাত ১১টার দিকে হানাদারেরা স্ক্রোলিং করে নিরাপদ দুরত্বে এসে হেঁটে বেড়া নদী পার হয়ে ঢাকা যাবার উদ্দেশ্যে পালিয়েছে। পরে জানা গেলো, পাকি হানাদারেরা বেড়া ঘাটে গিয়ে ভেড়াকোলা গ্রামের হলদারদের নৌকায় নদী পার হয়ে নগরবাড়ি ঘাট হয়ে ঢাকা যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।
ধীতপুরের যুদ্ধে বেড়ার এস এম আমির আলীর গ্রুপের বৃশালিকা গ্রামের জনাব আব্দুল খালেক ও ছেচানিয়া গ্রামের আমজাদ হোসেন শহিদ হয়েছেন এবং অন্যান্য গ্রুপের ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েছেন। স্থানীয় দু’জন পথচারী গোলাগুলির সময় গুলি লেগে ওয়াপদা বাঁধের উপর মারা গেছেন। ধীতপুর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমরা জামিরতা হাই স্কুলে ক্যাম্প করে অবস্থান নিয়েছিলাম। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এ শাহজাদপুর উপজেলা হানাদারমুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধা প্রশাসন গড়ে উঠে। আব্দুল বাকি মির্জা শাহজাদপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাধিনায়ক ও থানা প্রশাসক মনোনীত হন। তিনি সিও (ডেভ) অফিসে বসতেন। শাহজাদপুর থেকে সারা উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্ত খরচ বহন করতেন।
পরে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়।
জুলফিকার আলী ভুট্টো ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে আমাদের জাতির পিতাকে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত করে দেন। জাতির পিতা ওইদিনই লাহোর থেকে সকালে বিমানে যাত্রা করে বিকেলে ইংল্যান্ডের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বাঙালিদের জাতির পিতাকে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে সংবর্ধনা দেন। জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি ব্রিটিশদের বিশেষ বিমানযোগে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। বাংলাদেশে আসার পথে ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ভারতে যাত্রাবিরতি করেন। তারপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে আসলেন। ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে জাতির পিতা প্রথমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং পরক্ষণেই রাষ্ট্রপতি পদের ইস্তফা দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রথা চালু করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। জাতির পিতা আমাদেরকে অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমাদের গ্রুপ ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ এ (রোববার) সিরাজগঞ্জ সদরের ইব্রাহিম বিহারীর বাসায় অস্ত্র জমা নেওয়ার ক্যাম্পে অস্ত্র ও গোলাবারুদ্ধ জমা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব শেষ করলাম। সরকারের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য ন্যাশনাল মিলিশিয়া ক্যাম্প করা হলো। আমি ন্যাশনাল মিলিশিয়া ক্যাম্পে ভর্তি না হয়ে বাড়িতে চলে এলাম। কয়েকদিন পর রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমার বড় দাদা দেবেন্দ্র নাথ সান্যাল এর কাছ থেকে অষ্টম শ্রেণীর অটোপাশের টিসি নিয়ে শাহজাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করলাম।
লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার।
ঠিকানা : বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবেশ চন্দ্র সান্যাল, পিতা : দ্বিজেন্দ্র নাথ সান্যাল, মাতা : নিলীমা রানী সান্যাল, গ্রাম ও ডাকঘর : রতন কান্দি, ইউনিয়ন : হাবিবুল্লাহনগর, উপজেলা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ। গেজেট নং-বে-সামরিক সিরাজগঞ্জ : ১৬৭৯। ভারতীয় প্রশিক্ষণ : এফএফ নম্বর : ৪৭৪২। সমন্বিত তালিকা জেলাভিত্তিক : ১৬১১, উপজেলা ভিত্তিক : ১৫১, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম নম্বর : ০১৮৮০০০১৪১১।